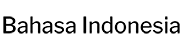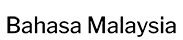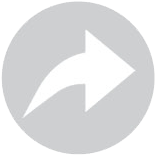চলেন গেলেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, আক্রান্ত ছিলেন করোনাভাইরাসে
2020.05.14
ঢাকা
চলে গেলেন দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (৮৩)। মৃত্যৃর পর জানা গেছে তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন।
বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা ৫৫ মিনিটে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তিনি মারা যান বলে বেনারকে জানান তাঁর ছেলে আনন্দ জামান।
“বাবার করোনা পরীক্ষার জন্য আজ সকালে একবার নমুনা নিয়েছিল। মৃত্যুর পর বিকেলে আবারও নমুনা সংগ্রহ করা হয়,” জানিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে আনন্দ বেনারকে জানান, “কিছুক্ষণ আগে আমাদের জানানো হয়েছে, তিনি করোনা পজিটিভ ছিলেন।”
করোনাভাইরাস ছাড়াও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান হৃদরোগ, কিডনি এবং ফুসফুসের জটিলতায় ভুগছিলেন। আনন্দ বলেন, “শেষ দিকে তাঁর রক্তেও সংক্রমণ দেখা দিয়েছিল।”
আনন্দ জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবার কারণে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মরদেহ কভিড ১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনেই দাফন করা হবে।
“জানাজায় অংশগ্রহণ বা সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তাঁর মরদেহ শহীদ মিনারে নেওয়ার সুযোগ নেই,” বলেন আনন্দ জামান।
জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মৃত্যুতে দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধী দল জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের৷
শেখ হাসিনা বলেন, “তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে হারাল। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতি তাঁর অবদান চিরদিন স্মরণ রাখবে। তাঁর মৃত্যু জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।”
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছিলেন দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক। ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।
রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা বাসস জানিয়েছে, ১৯৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পরিবারের সঙ্গে তিনি তৎকালীন পূর্ব বাংলায় চলে আসেন।
তিনি স্ত্রী সিদ্দিকা জামান, দুই মেয়ে রুচিবা ও শুচিতা এবং একমাত্র ছেলে আনন্দসহ অংসখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
তিনি ছিলেন বাতিঘর
কয়েক প্রজন্মের প্রিয় শিক্ষক ড. আনিসুজ্জামান ‘আনিস স্যার’ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ছয় দশক ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করেন।
“অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছিলেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের বাতিঘর। তিনি আমাদের তৈরি করেছেন। জাতীয় মানস গঠনে এবং বাঙালি চেতনার প্রাণ সঞ্চারে তিনি ছিলেন অগ্রবর্তী নেতা,” বেনারকে বলেন কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।
অধ্যাপক যতিন সরকার বেনারকে বলেন, “বাংলাদেশের মনন সাহিত্যে তাঁর তুল্য মানুষ আর একজনও রইল না। তিনি “মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য” গ্রন্থে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বিষয়টি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা একেবারেই নতুন।”
সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বেনারকে বলেন, “তিনি ছিলেন ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে এবং দেশের সব প্রগতিশীল আন্দোলনের অগ্রবর্তী মানুষদের একজন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে গঠিত গণআদালতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন মেধাবী শিক্ষাবিদ এবং গুণিজনকে হারাল।”
আনিসুজ্জামানের মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য পবিত্র সরকার বেনারকে বলেন, “আনিসুজ্জামানের চলে যাওয়ার খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি। দুই বাংলার বাঙালিদের মাথার ওপর থেকে ছাদটা সরে গেলো। দক্ষিণ এশিয়ার বিবেকের কন্ঠস্বর চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেলো।”
ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, “উনি আমার অগ্রজ। স্নেহ পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। ফলে স্নেহের অভাবটা বোধ করছি। বিশেষ করে এখন তো স্নেহ করার মানুষও বিশেষ আর নেই।”
আনিসুজ্জামান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক। পরে সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট ডক্টরাল ফেলো এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের কমনওয়েলথ অ্যাকাডেমিক স্টাফ ফেলো ছিলেন।
তিনি জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও ইউনিভার্সিটি অব প্যারিস, নর্থ ক্যারালাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ব ভারতীর ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ড. কুদরাত-ই-খুদাকে প্রধান করে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন তিনি।
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ভাষা আন্দোলন, রবীন্দ্র উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন, ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তিনি ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করেন এবং পরে ভারতে গিয়ে শরণার্থী শিক্ষকদের সংগঠন ‘বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগ দেন।
অবদানের স্বীকৃতি
আনিসুজ্জামান শিক্ষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য একাধিক পুরস্কার লাভ করেছেন। প্রবন্ধ গবেষণায় অবদানের জন্য ১৯৭০ সালে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। শিক্ষায় অবদানের জন্য তিনি ১৯৮৫ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন।
শিক্ষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মভূষণ পদক প্রদান করা হয়। সাহিত্যে অবদানের জন্য ২০১৫ সালে তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হয়।
এ ছাড়া ২০০৫ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. ডিগ্রি এবং ২০১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক লাভ করেন।
আনিসুজ্জামান অন্তত অর্ধশত গ্রন্থের লেখক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে তাঁর গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।
তাঁর রচনাবলির মধ্যে ‘মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য,’ ‘মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র,’ ‘স্বরূপের সন্ধানে,’ ‘আঠারো শতকের বাংলা চিঠি,’ ‘পুরোনো বাংলা গদ্য,’ ‘আমার একাত্তর,’ ‘মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর,’ ‘কাল নিরবধি,’ ‘স্মৃতিপটে সিরাজুদ্দীন হোসেন,’ ‘শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্মারকগ্রন্থ,’ ‘নারীর কথা,’ ‘মধুদা,’ ‘ফতোয়া’, ‘ওগুস্তে ওসাঁর বাংলা-ফারসি শব্দসংগ্রহ,’ ও ‘আইন-শব্দকোষ’ অন্যতম।
প্রতিবেদনে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন কলকাতা থেকে পরিতোষ পাল।