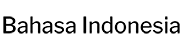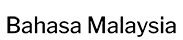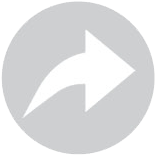সামান্য মজুরির চা শ্রমিকদের দূর্দশায় ভরা জীবন
2016.01.15
 সিলেটের একটি চা বাগানে কর্মরত নারী চা শ্রমিক।
সিলেটের একটি চা বাগানে কর্মরত নারী চা শ্রমিক।
দীপক লোহাড়। বয়স ৪৩। চেহারা ও শরীরের জীর্ণ দশা দেখলে মনে হয়, বয়স সত্তরের কাছাকাছি। কাজ করেন সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগানে। সকাল সাড়ে আটটায় বাসা থেকে বের হন, ফিরেন বিকেল সাড়ে চারটায়। দৈনিক মজুরি ৬৯ টাকা।
দীপকের ভাষায়, “খাইয়া, না-খাইয়া কোনোমতে বাইচা আছি-গো দাদা। যতক্ষণ গতরে শক্তি আছে, ততক্ষণ না হয় খাটলাম। অল্প একটু অসুস্থ হইলেই-তো কাজ করতে পারি না।“
তখন বাগান থেকে বলে, “কাজে যাও, আর না পারলে নাম কাটাও”।
“নাম কাটাইমু কেমনে, কন-গো দাদা। নাম কাটাইলে-তো ৬৯ টাকাও পাইমু না। আর এই টাকায় কিভাবে চাইরজনের সংসার চলে, কইতে পারেন?“
দীপকের পরিবারে স্ত্রী, দুই ছেলে আর এক মেয়ে।
“পোলা-মাইয়া অনেক সময় স্কুলের খাতা-কলম চায়, দিতে পারি না। ভালো-মন্দ খাইতি চায়, দিতে পারি না।“ আক্ষেপ করলেন দীপক।
গত বৃহস্পতিবার সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগানে কথা হয় দীপকের সঙ্গে। তখন তিনি এভাবেই নিজেদের অসহায়ত্ব ও মানবেতর জীবনযাপনের কথা জানান।
দেশে এখন মোট চায়ের চাহিদা ৫ কোটি কেজি। ১৬৮টি বাগান থেকে উৎপাদন হয় প্রায় সাড়ে ৬ কোটি কেজি। তাই চাহিদা মিটিয়ে চা রফতানি করা হয়।
দেশের এই শিল্পের সাথে জড়িত প্রায় ১২ লাখ শ্রমিক। এমনিতেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা সূচকে পিছিয়ে চা বাগানের শ্রমিকরা। অন্য কোন কাজ না জানায় চা বাগানের বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ নেই তাদের।
সিলেট শহরের খুব কাছেই চা বাগান। শহরের আম্বরখানা থেকে ওসমানী আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরে যাওয়ার সড়কে মাঝামাঝি স্থানে লাক্কাতুরা চা বাগান।
হাতের বামদিকে চা শ্রমিকদের থাকার জায়গা। ছড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছি চা পল্লীতে। পথে দেখা রিনা গোয়ালার সঙ্গে। তিনি ছড়ায় গোসল করে ঘরে ফিরছিলেন।
নোংরা এ ছড়ায় গোসল যে করলেন, অসুখ হবে না- এমন প্রশ্নে হেসে রিনার উত্তর, “আমরার আবার অসুখ। অসুখ হইলেই কী, আর না হইলেই কী! এখানে গোসল করা ছাড়া আর উপায় আছে?“
একটু এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, খোলা জায়গায় ছড়ার পারে পায়খানার ব্যবস্থা। প্রশ্রাব-পায়খানা গিয়ে পড়ছে ছড়ায়, যে ছড়ায় একটু আগে গোসল করে এসেছেন রিনা।
অভাবে চিকিৎসা নিতে পারেন না
চা পল্লীর একটু ভেতরে যেতেই দেখা হয় কান্তমনি লোহাড়ের (৫৬) সঙ্গে। অসুস্থ হয়ে ঘরে বসে আছেন আর কাতরাচ্ছেন।
ডাক্তার দেখাননি?-এমন প্রশ্নের উত্তরে কান্তমনি বলেন, “ডাক্তার কই দেখাইমু। এখানে হাসপাতাল বলতে যা বুঝায় তা-তো নাই। ডাক্তার নাই, আছে মিডওয়াইফ। গেলে-তো খালি প্যারাসিটামল ছাড়া আর কোনো ঔষধ দেয় না।“
বেশি সমস্যার কথা বললে কয়, “সরকারী হাসপাতালে যাও।”
“এখান থেকে সরকারী হাসপাতালে যাইতে হইলেও তো অন্তত ৮০ টেকা লাগে। গেলেই হইলো, ডাক্তার কত ধরণের পরীক্ষা যে করতে দেয়। টেকা পামু কই? টেকা না থাকায় পরীক্ষা করাইতে পারি না, ঔষধ কিনতে পারি না। এর চেয়ে না যাইয়া, মরি যাওয়াই ভালো,“ জানান কান্তমনি।
শুধু দীপক লোহাড়, রিনা গোয়ালা, কিংবা কান্তমনি লোহাড় নয়, এ যেন সব চা শ্রমিকের জীবনের নিয়তি। ওই দিন অন্তত ১০-১২ জন চা শ্রমিকের সঙ্গে কথা হয় । তাঁদের কথায় উঠে আসে চা শ্রমিকদের জীবনের এমন রূঢ় বাস্তবতা।
শ্রম মন্ত্রণালয় তিন শ্রেণির চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৬৯, ৬৭ ও ৬৬ টাকা নির্ধারণ করেছে। আগে তাদের মজুরি ছিল যথাক্রমে ৬২, ৬০ ও ৫৯ টাকা। সঙ্গে সপ্তাহে ৩ কেজি রেশনের চাল ও আটা। এ দিয়ে পরিবার নিয়ে তিন বেলা খাবার জোটে না শ্রমিকদের।
চা শ্রমিকের সন্তানদের সমাজের মূল স্রোতে উঠে আসা যে কত কঠিন তার অনেকটা বিষয় জানা গেল চিত্তরঞ্জন রাজবংশীর কাছে। তিনি চা শ্রমিকের সন্তান। স্নাতকোত্তর পাশ করে এখন শিক্ষকতা করছেন গোয়াইনঘাট ডিগ্রি কলেজে।
তিনি জানান, চা বাগানের শ্রমিকের রাজবংশী, গোয়ালাসহ অনেক টাইটেলধারীদের আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোটার আওতায় নেওয়া হয় না। দুই বছর আগে মনি গোয়ালা নামে তাঁর পরিচিত এক ছাত্রী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর টাইটেলের জন্য তাঁকে সনদ দেওয়া হয়নি। ফলে সে আর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি।
এখন পর্যন্ত সারাদেশের চা বাগানের শ্রমিকদের সন্তানদের মধ্যে মাত্র ২০ জন স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন।
চিত্তরঞ্জন বলেন, এখন বাগানে শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। অনেকে ঋণ করে হলেও ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা করাতে চান। কিন্তু ব্যাংকে গেলে ঋণ পাওয়া যায় না। কারণ যে জমিতে চা শ্রমিকেরা বাস করেন তা তাঁদের মালিকানায় নাই।
“অল্প শিক্ষিতদের ছোটোখাটো চাকরি পাওয়া কঠিন। আগে কৃষিজমিতে চাষ করে কেউ কেউ ভালো জীবনধারণ করতেন। এখন হবিগঞ্জের চানপুর ও বেগমখানসহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রকল্পের নামে সেটাও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে,“ জানান চিত্তরঞ্জন ।
প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরতে চায় কিছু দাবি
আগামী ২১ জানুয়ারি সিলেটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাবেন। এ সময় চা শ্রমিকেরা তাদের কিছু দাবি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরতে চান।
এগুলোর মধ্যে রয়েছে ভূমি অধিকার, শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের কোটাভিত্তিক চাকরি, বাগানে সরকারী বিদ্যালয়, মজুরি বোর্ডের আওতায় এনে মজুরি নির্ধারণসহ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ন্যায্য অধিকার দেওয়া।
“শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেওয়া হয় না, বাসস্থান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরাজীর্ণ, স্বাস্থ্যখাতে ডিসপেনসারিতে চিকিৎসক ও পর্যাপ্ত ওষুধ নাই, বিভিন্ন কায়দায় শ্রমিকদের কৃষিজমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে-এ রকম বাস্তবতায় আমরা কোনো রকমে বেঁচে আছি,“ বেনারকে জানান বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সিলেট ভ্যালির সভাপতি রাজু গোয়ালা ।
চা শ্রমিকদের পল্লী থেকে বের হয়ে আসার সময় চা শ্রমিক বিমল গোয়ালা বলেন, “দাদা, দুই মুঠো ভাত খাইতে যাঁদের মুরোদ নাই, তাঁরা গাড়ি ভাড়া নিয়া হাসপাতালে যাইবো কেমনে? টেকা-পয়সার অভাবে বাচ্চা-কাচ্চা পড়াইতে পারি না। আগে জমিতে ক্ষেত-খামার করিয়া কিছু পাইতাম, এখন জমিও কাড়িয়া নেওয়ার কাজ শুরু হইছে। আমরা আজীবন এইরকম থাকমুনি-গো দাদা?“
চা শ্রমিকদের নানাবিধ সমস্যা ও জীবনমান নিয়ে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য প্রকৌশল ও চা প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. মোজাম্মেল হক বেনারকে বলেন, 'চা শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম। তাঁদের জীবনমান অত্যন্ত নিম্নমানের। তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থাসহ সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়ন খুবই জরুরি'।
ফিরে দেখা
তথ্যপ্রমান বলছে, চা শিল্প স্থাপিত হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়েই। পাহাড়ি জায়গা বেছে নেয়া হয় চা শিল্পের জন্য। শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় সমাজের সবচেয়ে নিচু শ্রেণির হরিজন, কোল, মুন্ডা, কৈরি, চন্ডাল, সাঁওতাল প্রভৃতি সমপ্রদায়ের লোকজনদের যাদের নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতি থাকলেও তা উপেক্ষিত।
ব্রিটিশেরা চা শ্রমিকদের মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খন্ডের রাত্রি, ডোমকা, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এনেছিল। চা বাগান ছাড়া অন্য কোন কাজ জানা নেই এদের।
বাংলাদেশে চা শিল্পের ইতিহাস ১৫০ বছরের। সিলেটে চা বাগান তৈরির শুরুর দিকে উন্নত জীবনযাপনের আশা নিয়ে জন্মমাটি ছেড়ে চা বাগানে কাজ করতে আসে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের অভাবী মানুষ।
কিন্তু কাজে এসে তাদের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যায়। তারা ফিরতে চায় নিজের দেশে। এসময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নির্বিচারে হাজার হাজার চা শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে। ১৯২১ সালের ২০ মের সেই রক্তাক্ত পরিণতিতে চা শ্রমিকদের দেশে ফেরার স্বপ্নও শেষ হয়ে যায়।