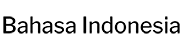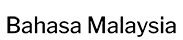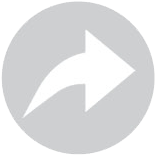দেশে মানবাধিকার হুমকির মুখে, সংসদ অকার্যকর: সুপ্রিম কোর্ট
2017.08.02
ঢাকা
 বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভবন। আগস্ট ০২, ২০১৭।
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভবন। আগস্ট ০২, ২০১৭।
বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি হুমকির মুখে, সংসদ অকার্যকর এবং প্রশাসনে অব্যবস্থা বিরাজমান বলে মন্তব্য করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালাত।
গত মঙ্গলবার সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে দেওয়া ৭৯৯ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায়ে আদালতের এইসব পর্যবেক্ষণ প্রকাশিত হয়।
উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, “দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি হুমকির মুখে, দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব বেড়েছে, সংসদ কার্যকর নয়, কোটি কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত এবং প্রশাসনেও তীব্র অপব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে।”
তবে এসব বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।
যোগাযোগ করা হলে পূর্ণাঙ্গ রায় না পড়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। বেনারকে তিনি বলেন, এখনই এ বিষয়ে কথা বলবেন না।
নাগরিকদের জীবন ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে অনিরাপদ হয়ে উঠছে মন্তব্য করে রায়ে বলা হয়, “আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, যার ফলশ্রুতিতে একটি বিকলাঙ্গ সমাজ তৈরি হয়েছে; যেখানে ভালো মানুষ আর ভালো কিছুর স্বপ্ন দেখছে না। কিন্তু খারাপ মানুষগুলো অবৈধ সুবিধা আদায়ে মরিয়া হয়ে উঠছে।”
“এমন অবস্থায় নির্বাহী বিভাগ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ছে। এর ফলে আমলাতন্ত্রে দক্ষতা বলে কিছু থাকবে না,” মন্তব্য সর্বোচ্চ আদালতের।
আদালতের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, “স্বাধীনতার ৪৬ বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানেই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করাতে পারিনি। কোথাও কোনো চেক অ্যান্ড ব্যালান্স নেই; কর্মক্ষেত্রে নজরদারি নেই; যে কারণে পদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ক্ষমতার অপব্যবহারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে ও ইচ্ছেমতো ক্ষমতা প্রয়োগের দুঃসাহস দেখাচ্ছে।”
বিচার ব্যবস্থার ওপরও আলোকপাত করে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, “অবিরাম চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বিচার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের একমাত্র অপেক্ষাকৃত স্বাধীন অঙ্গ। যদিও তা নিমজ্জিত হচ্ছে কিন্তু প্রতিকূলতা মাড়িয়ে টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।”
পর্যবেক্ষণে আরও উল্লেখ করা হয়, “কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে বিচার বিভাগের জন্যও বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়। এখনো উচ্চ আদালতের বিচারকদের নির্বাচন ও নিয়োগের জন্য কোনো আইন করা হয়নি। বিচারকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।”
ফিরছে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল
সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত করে ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সংবিধানে ষোড়শ সংশোধনী আনে জাতীয় সংসদ। এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা রিটের প্রেক্ষিতে গত বছরের ৫ মে ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট। এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিলও গত ৩ জুলাই খারিজ করে দেয় আপিল বিভাগের সাত সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ।
পূর্ণাঙ্গ রায়ে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের ছয়টি ধারা পুনর্বহালের মাধ্যমে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অসদাচরণ তদন্ত ও অপসারণের সুপারিশ করার ক্ষমতা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুনঃস্থাপিত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি এবং দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারককে নিয়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে।
প্রকাশিত রায়ে বিচারকদের জন্য ৩৯ দফা আচরণবিধিও প্রণয়ন করা হয়েছে।
রিটকারী পক্ষের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বেনারকে বলেন, “সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ের মাধ্যমে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃস্থাপন হয়ে গেছে। এখন থেকে কোনো বিচারককে অপসারণের প্রয়োজন হলে, তা করা হবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে।”
এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেন, “সংবিধানের যে কোনো ধারা সংশোধন করা বা বাদ দেওয়া সবটাই সংসদের ব্যাপার। কোর্ট যদি নিজেই রিস্টোর (পুনঃস্থাপন) করে, তাহলে সংসদের থাকার কোনো দরকার হয় না।”
“তবে সরকার এখনো চাইলে এ রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন করতে পারে। রায়ের সার্টিফায়েড কপি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এ আবেদন করার সুযোগ রয়েছে” বেনারকে বলেন সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ।
তবে অ্যাটর্নি জেনারেল বেনারকে বলেন, “বিষয়টি নির্ভর করছে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর।”
বিচারকদের জন্য ৩৯ দফা আচরণবিধি
সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান কার্যকর করতে উচ্চ আদালতের বিচারকদের জন্য ৩৯ দফার আচরণবিধি চূড়ান্ত করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।
এতে বিচারকদের পেশাদারি ও নৈতিক মানদণ্ড থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পর্যন্ত সর্বস্তরের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এগুলো অনুসরণ না করা হলে তা গুরুতর অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে।
পূর্ণাঙ্গ রায়ে বলা হয়, কোনো বিচারকের আচরণের বিষয়ে অভিযোগ পেলে প্রধান বিচারপতি এবং দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারককে নিয়ে কাউন্সিল গঠন করবেন। প্রধান বিচারপতি বা অন্য কোনো বিচারক অস্বীকৃতি জানালে কিংবা কাউন্সিলের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠলে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ বিচারক ওই কমিটির সদস্য হবেন।
প্রাথমিক তদন্তে যদি অভিযোগের প্রমাণ মেলে তবে প্রধান বিচারপতি বিষয়টি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন। কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দ্রুত এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে খতিয়ে দেখতে হবে।
একজন বিচারক উচ্চ মানের আচার প্রতিষ্ঠা, প্রয়োগ ও রক্ষণে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি চার বিভাগের ন্যায়পরায়ণতা এবং স্বাধীনতা বজায় থাকার মতো মান মেনে চলবেন। তাঁকে সংবিধান ও আইন মানতে হবে। তিনি সব সময় বিচার বিভাগের ওপর মানুষের আস্থা বাড়ার মতো কাজ করবেন। পারিবারিক, সামাজিক বা অন্য কোনো সম্পর্কের কাউকে বিচারিক আচরণ প্রভাবিত করতে দেবেন না।
বিধিমালায় দলীয় স্বার্থ, জনবিক্ষোভ বা সমালোচনায় বিচারককে প্রভাবিত না হতে বলা হয়। বিচারক কোনো মামলার বা বিচারাধীন বিষয় নিয়ে জনসমক্ষে মন্তব্য করতে পারবেন না। দ্রুত বিচার শেষ এবং রায় দেওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই তাতে স্বাক্ষর করবেন।