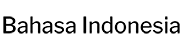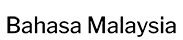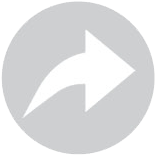রোহিঙ্গা সংকট: আগের অঙ্গীকার পূরণ করেনি মিয়ানমার
2017.11.20
ঢাকা
 টেকনাফের খারাংখালী সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের দিকে ছুটছেন রোহিঙ্গারা। নভেম্বর ১৪, ২০১৭।
টেকনাফের খারাংখালী সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের দিকে ছুটছেন রোহিঙ্গারা। নভেম্বর ১৪, ২০১৭।
মিয়ানমার সরকার ১৯৭৮ এবং ১৯৯২ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বা ইশতেহার অনুযায়ী সেসব আশ্বাস পূরণ না করে বারবার উল্টো পথে হেঁটেছে দেশটি।
১৯৯২ সালে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের যৌথ ইশতেহার ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি দুটির কপি বেনারের হাতে রয়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে আগামী ২২ ও ২৩ নভেম্বর নেপিডোতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হতে যাচ্ছে। মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তিন্ত সোয়ের সঙ্গে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এই বৈঠক করবেন।
বাংলাদেশ সরকার আশা করছে, ওই বৈঠকে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসবে।
“দেখুন, আমরা শরণার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য বহুদিন ধরে বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে আসছি। এখনো একটি স্থায়ী ও টেকসই সমাধানের চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান চায়,” বেনারকে জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া অনুবিভাগের মহাপরিচালক মঞ্জুরুল করিম খান।
এর আগে মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওহন গিও এবং বাংলাদেশের প্রয়াত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আ স ম মোস্তাফিজুর রহমানের মধ্যে ১৯৯২ সালের ২৮ এপ্রিল যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষর হয়। তাতে রোহিঙ্গাদের ‘মিয়ানমার সমাজের অংশ’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া শরণার্থীদের নিজস্ব বসতবাড়িতে নিরাপদে ও স্বেচ্ছায় পুনর্বাসনে একমত হয়েছিল উভয়পক্ষ।
১৯৯২ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফরের সময় যৌথ ইশতেহারে মিয়ানমার সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, রোহিঙ্গা সমস্যার পুনরাবৃত্তি হবে না এবং এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করবে।
যদিও সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ‘অবৈধ বাংলাদেশি’ হিসেবে আখ্যায়িত করছে। গত ১৬ নভেম্বর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসনের সঙ্গে বৈঠকে মিয়ানমারের সেনাপ্রধান সিনিয়র জেনারেল মিন অং হিয়াং রোহিঙ্গা মুসলিমদের ‘বাঙালি’ বলে অভিহিত করেন বলে জানিয়েছে রেডিও ফ্রি-এশিয়া।
বেনার নিউজের সহযোগী প্রতিষ্ঠান রেডিও ফ্রি-এশিয়া জানায়, সেনাপ্রধান হিয়াং বলেন, মিয়ানমারের প্রকৃত নাগরিকেরা গ্রহণ করলেই কেবল যারা রাখাইন থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে তাদের গ্রহণ করা হবে।
ইশতেহারে যা বলা হয়
১৯৯২ সালে ইশতেহারের আট দফায় বলা হয়, শরণার্থী সমস্যা যাতে পুনরায় না ঘটে এবং এর স্থায়ী ও ব্যাপক সমাধানের জন্য দুই সরকার একসঙ্গে কাজ করবে।
এর ছয় দফায় উল্লেখ রয়েছে, প্রত্যাবাসন হবে নিরাপদ ও স্বেচ্ছাধীন। মিয়ানমারের অধিবাসীদের তাদের মূল নিজস্ব বসতভিটায় পুনর্বাসিত করা হবে এবং ‘মিয়ানমার সমাজের অংশ’ হিসেবে তারা সেখানে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে।
ইশতেহারের তিন দফায় বলা হয়, মিয়ানমার সরকার তার নাগরিকদের বাংলাদেশে পালিয়ে আসা বন্ধ করতে সকল ব্যবস্থা নেবে এবং ইতিমধ্যে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা নাগরিকদের স্বেচ্ছায় ও নিরাপদে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে।
১৯৭৮ সালের চুক্তিকে যা বলা আছে
১৯৭৮ সালের ৭-৯ জুলাই মিয়ানমার (বার্মা) ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ে বৈঠকের পর স্বাক্ষরিত প্রত্যাবাসন চুক্তিতে মিয়ানমার থেকে যারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে তাদের ‘বৈধ নাগরিক’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মিয়ানমারের বৈধ নাগরিক হিসাবে প্রমাণ করতে জাতীয় রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রদর্শনের কথা বলা হয়।
চুক্তিতে আরও বলা হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে যেসব শরণার্থী রাখাইনে তাদের বসবাসের প্রমাণ করতে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা দলিল দেখাতে পারবে এবং তাদের নিকটাত্মীয়ের নাম-ঠিকানা বলতে পারবে তাদের প্রত্যাবাসন করা হবে।
চুক্তিতে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ৩১ আগস্ট ১৯৭৮ শুরু হয়ে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে শেষ করার কথা বলা হয়।
“১৯৯২ সালে তারা আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, রোহিঙ্গা সমস্যা যাতে আর না হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু তারা তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। রাখাইনে অবস্থারও কোনো উন্নতি হয়নি। রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে,” বেনারকে বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।
মিয়ানমার সরকারের রাষ্ট্রীয় পরামর্শক অং সান সু চির সঙ্গে গত ২৪ অক্টোবর সাক্ষাতের প্রসঙ্গ টেনে আসাদুজ্জামান খান বলেন, “সু চি আমাকে জানান যে, তারা (রোহিঙ্গারা) রাখাইনে থাকতে চায় না। ফিরিয়ে নেওয়ার পর আবার বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। তোমরা তাদের বলো তারা আর যেন তোমাদের ওখানে পালিয়ে না যায়।”
সুচির এই বক্তব্য প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। তোমাদের এখানে পারে না। তাই যায় বা যেতে বাধ্য হয়। মিয়ানমারের পরিস্থিতির উন্নতি হলে ওরা বাংলাদেশে যাবে না।”
যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে যেসব বিষয়ে সমঝোতা হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে পরবর্তীতে কফি আনান কমিশনের রিপোর্টের প্রসঙ্গ একতরফাভাবে বাদ দেয় মিয়ানমার।
১৯৯২ সালের পর ২০১২ সালে একজন রাখাইন নারীকে একজন রোহিঙ্গা পুরুষ ধর্ষণ করেছে মর্মে অভিযোগ ওঠার পর রাখাইনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। তখন কয়েক হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে।
২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর মিয়ানমার নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর আল-ইয়াকিন নামক জঙ্গি গোষ্ঠীর আক্রমণের পর আরও ৮০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে।
এ বছরের ২৫ আগস্ট জঙ্গি গোষ্ঠী আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মির বিরুদ্ধে মিয়ানমার সেনাবাহিনী অভিযান শুরুর আগ পর্যন্ত প্রায় ৪ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অবৈধভাবে অবস্থান করছিল। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএসএইচসিআর–এর হিসেবে, ২৫ আগস্টের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৬ লাখ ২০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।
বাংলাদেশ যা চায়
পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবাসনসহ সমস্যাটির একটি স্থায়ী ও টেকসই সমাধানে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিশ্চয়তা চাইবে। বাংলাদেশের পক্ষে এত বিশাল জনগোষ্ঠীর চাপ নেওয়া বাংলাদেশের পক্ষে যে সম্ভব নয় তা বাংলাদেশ জাতিসংঘসহ সকল ফোরামে জানিয়ে দিয়েছে।
গত বুধবার জাতীয় সংসদে এক লিখিত বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, “রোহিঙ্গা সমস্যার শুরু মিয়ানমারে আর এর সমাধান মিয়ানমারকেই করতে হবে।”
সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপু মনি বেনারকে বলেন, “রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ এর আগে মিয়ানমারের সঙ্গে বিভিন্ন ‘কনফিডেন্স বিল্ডিং’ এর উদ্যোগ নিয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রাখাইন রাজ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছিলো। কিন্ত সেসব উদ্যোগ সফল হয়নি। তবে বাংলাদেশ বিশ্ব জনমত সঙ্গে নিয়ে মিয়ানমারের অন্যায় ঠেকাতে চাপ অব্যাহত রাখছে।”
১৯৭৮ ও ১৯৯২ সালের চুক্তির পরও রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত থাকা প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা—আইওএম এর সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তা আসিফ মুনীর বেনারকে বলেন, “রোহিঙ্গারা শত শত বছর ধরে সেখানে বসবাস করলেও মিয়ানমারের নাগরিকেরা কখনো তাদের মানসিকভাবে গ্রহণ করেনি।”
মুনীর বলেন, “আর সে কারণেই সমস্যা ক্রমেই জটিল হয়েছে। মূল সমাজ যখন একটি জনগোষ্ঠীকে গ্রহণ না করে, তখন সরকারও তাদের গ্রহণ করতে চায় না। আমি মিয়ানমারের কিছু গ্রামে ‘মুসলিম-মুক্ত গ্রাম’ লেখা সাইনবোর্ডে দেখেছি।”